বাংলা সাহিত্য প্রাচ্য সাহিত্যসম্পদ থেকে বঞ্চিত কেন?
- আপডেট টাইম: সোমবার, ১৩ জানুয়ারী, ২০২৫

মোঃ খলিলুর রহমান।। সাহিত্য সংস্কৃতি ভাষা ও সাহিত্যভিত্তিক রাজনীতির সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন পাক ভারত বাংলাদেশ উপমহাদেশে অতীত থেকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে অরক্ষিত নয়। বাংলা সাহিত্যের কোনো না কোনো পর্যায়ে পূর্বসূরিতা আরবি ফারসি ও উর্দু সাহিত্য বনাম হিন্দি সংস্কৃত সাহিত্য প্রভাব ব্যাখ্যাসাপেক্ষ বিষয়। হাফিজ রুমি সাদি আত্তার ফেরদৌসী খৈয়াম সংযোগটা পরবর্তীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল কালিদাস বাল্মিকী, শেলি কীটস বায়রন এর দিকে।
এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার চেষ্টা চলে যে, বেদান্ত সংস্কৃত বাংলার পূর্বসূরী। তাই রাধাকৃষ্ণ ও বৈষ্ণব কাহিনি আমাদের উত্তরাধিকার। কী করে সম্ভব? ইতিহাসের ধারাবাহিকতা তথা বাস্তবতা তা বলে না। তা হচ্ছে চর্যাপদের সাহিত্য দর্শন বৌদ্ধ পালি সংস্কৃতি ও সাহিত্য এ ধারণাকে Contradict করে। অথচ আর্য ও আর্য সংস্কৃতি তো এ উপমহাদেশীয় সম্পদ নয়। ধর্ম দর্শন ও ধর্মীয় সংস্কৃতি সূত্রে আরবি ফারসি আমাদের সগোত্রীয়। পাশাপাশি উপমহাদেশ অর্থাৎ পাক ভারত ও ইরান আরব-এর চিন্তাধারা আমাদের ভাব ও সংস্কৃতিতে অপূর্ব মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। মোগল পাঠানের পর এ দেশে এলো ইংরেজ। ইংরেজরা আমাদের পাশ্চাত্যমুখী করেছে। এশিয়া বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যমুখী সাহিত্য সংস্কৃতি থেকে আমরা ইউরোপ আমেরিকার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি ঝুঁকে পড়ি। হিন্দু সাহিত্যিকদের প্রভাবিত ভারতীয় মুসলিম সাহিত্যিকরাও। ফলে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাবধারার প্রভাব আরবি ফারসি ভাবধারার প্রভাবকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে। এতে করে আমাদের সাহিত্যের ভাবধারা
গঠনে আরবি ফারসি তুর্কি অবদান ও অনুসৃতি আমরা আর দেখতে পাইনি।
ফারসি ইতিহাস বলে, ইরান তুরস ও উত্তর ভারতে ফারসি গদ্য ও পদ্য সাহিত্যের ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছর ধরে স্থিতিশীল ছিল। বিশ শতকের শুরুতে পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে ফারসি সাহিত্য ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।
ইসলামপূর্ব যুগের ফারসি সাহিত্য (৬৫০ খ্রিষ্টপূর্ব থেকে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তথা আড়াই হাজার বছর পূর্ব থেকে প্রায় ১ হাজার বছর) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ফারসি ভাষায় লিখিত হয়। সে সাহিত্যে ‘গাথা’ নামে ঐশ্বরিক সংগীত এবং ‘আবেস্তা’ নামে প্রাচীন ধর্মীয় রচনাবলী সংগ্রহ ছিল। মধ্যযুগে আবেস্তার অনুবাদ এবং ইরানের রাজদরবারে উপস্থাপিত মহাকাব্যগুলো।
১৯১৯ সালে সফল ফারসি লেখকদের মধ্যে সাদিক হিদায়াতের নিরাশাবাদী, ব্যাধিগ্রস্ততাভিত্তিক সাহিত্যকর্ম তরুণ প্রজন্মের লেখকদের ওপর প্রভাব ফেলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইরানের কবিতায় নতুন ধারা শুরু হয়। কতিপয় আধুনিক কবি নিমা ইউশিজের কবিতার আদর্শে পুরোনো ঐতিহ্য ভাঙতে শুরু করেন। এসব আধুনিক কবিরা অন্তমিলবিহীন ও ছন্দহীন কবিতা লেখা শুরু করেন। এ সময় মালাকাম খান এবং সাদি নাট্যকার পশ্চিমা ধারার নাটক লেখা শুরু করেন। আফগানিস্তানের বালখে আবির্ভাব ঘটেছে ১৩ শতকের জগদ্বিখ্যাত ফারসি কবি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমির। গজনভী সাম্রাজ্য ও তুর্কি সেলজুক সাম্রাজ্য ফারসিকে ধারণ করেছিল। খোরাসনের (আফগান) শাসক নাসির খসরু, প্লেটোর ‘রিপাবলিক’ গ্রন্থটি ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।
তুর্কি কবি ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত রুবাইয়াত, ফেরদৌসী, শেখ সাদি, হাফেজ শিরাজি, ফরিদ উদ্দিন আত্তার, নিজামী গঞ্জেভি, রুমি প্রমুখ ফারসি কবিরা পশ্চিমা সাহিত্যসহ বিশ্ব সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছেন। কুর্দি মৌখিক ও লিখিত সাহিত্য সমৃদ্ধ। ২০ শতকের শুরুতে কাব্য সাহিত্য এবং পরবর্তী সময়ে গদ্যের বিকাশ ঘটে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের কারণে। কুর্দি কবি আহমেদ ই হানি রচিত ‘মেম ও জিন’ রোমান্টিক মহাকাব্য। উল্লেখ্য, আরবি ফারসি কুর্দি সব সাহিত্যই সেসব জাতির সংস্কৃতিকে ধারণ ও লালন করে। দশম শতাব্দীতে পারস্য-তুর্কি সাম্রাজ্য বিস্তার ঘটায় পারস্য ইসলামি সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। এ সময় ফারসি ছিল ভারতীয় রাজভাষা। ফলে ফারসি শিল্পকর্ম সাহিত্য বিশেষত ‘গজল’ (রোমান্টিক কবিতা) উর্দু হিন্দিসহ ভারতীয় সাহিত্যকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছিল।
মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইসলামি সাহিত্যের প্রভাব বেশি। বখতিয়ার খলজির বঙ্গে মুসলিম রাজত্ব কায়েমের ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম ঘটে। ইসলামে ভাষা ও সাহিত্য প্রধানত আরবি, ফারসি, ভারতীয়, কুর্দি, তুর্কি ও বাংলা সাহিত্যে গঠিত ও বিকশিত। এ ধারার সবচেয়ে বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম ‘আরব্য রজনীর গল্প’। গল্পগুলো মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যে ফ্রেম গল্পের কৌশল ব্যবহার করে রচিত। গল্পের মূল চরিত্র শেরজাদ। যিনি তার স্বামী রাজা শাহরিয়ারকে তার গল্পের সঙ্গে বিনোদন দিয়ে নিজ জীবন বাঁচায়। দশম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত এসব গল্প রচিত হয়। আরব্য রজনীর গল্পগুলো ১৮ শতকে পশ্চিমা সাহিত্যে প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। কারণ ফরাসি অনুবাদক আ্যান্টোইন গ্যালান্ড গল্পগুলো অনুবাদ করেছিলেন। তন্মধ্যে ‘আলাদীনের জাদুর প্রদীপ’, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর এবং নাবিক সিন্দাবাদ বিশ্বজুড়ে পাঠকদের কাছে বেশ জনপ্রিয়।
আরবি সাহিত্যের শুরু পঞ্চম শতাব্দীতে। এ সময় এ ভাষা লিখিত রূপ পায় এবং আরবি সাহিত্যের বিকাশ সূচিত হয়। কুরআন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। ৬ শতকের শ্রেষ্ঠ আরবি কবি ইমরুল কায়েসের শ্রেষ্ঠ কাব্য মুয়াল্লাকা। তিনি ছিলেন কিন্দা উপজাতির যুবরাজ।
মির্জা গালিব, জওক, ইকবাল প্রমুখ উর্দু সাহিত্যে ভাস্বর হয়ে আছেন। আধুনিক উর্দু কবিতায় প্রধান কবি পাকিস্তানের আহমদ ফরাজ। যার কবিতায় হৃদয় নাচে। সংস্কৃত ভাষার সাহিত্যভান্ডার কাব্য ও নাটক ছাড়াও দার্শনিক তত্ত্ব এবং হিন্দু শাস্ত্রীয় রচনায় সমৃদ্ধ। প্রাচীন ভাষা সংস্কৃতে সাহিত্যের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে ঋগ্বেদের রচনার মাধ্যমে। ব্যাকরণবিদ পাণিনির সময় পর্যন্ত খ্রিষ্টপূর্ব ৬ থেকে ৪ শতাব্দীর পর ধ্রুপদী সংস্কৃত গ্রন্থগুলো আদর্শ হয়ে ওঠে। বৈদিক ধর্মের বিস্তৃত
রূপ বৈদিক সংস্কৃত। কিছু সংস্কৃত বৌদ্ধ গ্রন্থকে বৌদ্ধ সংস্কৃতি বলা হয়। আমরা জানি, সংস্কৃত মহাকাব্যগুলো বাল্মিকী রচিত রামায়ণ, ব্যাস রচিত মহাভারত, কালিদাসের কুমার সম্ভব, রঘুবংশ ও মেঘদূত কাব্য।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আজো সংস্কৃতে অনার্স পড়ানো হলেও অন্যান্য ভাষার জনপ্রিয়তার তুলনায় এ ভাষা এখন গণনায় আসেনা। পতঞ্জলির (২ হাজার বছর আগের যোগসূত্র গ্রন্থ প্রণেতা সংস্কৃত লেখক ও দার্শনিক) ভাষ্য হচ্ছে, সংস্কৃত ভাষাকে সুবিন্যস্ত করে তোলাই ছিল পাণিনীয় ব্যাকরণের কাজ। দেবভাষা সংস্কৃতকে মৃতভাষা বলার মতো পরিণতি কেন-এ নিয়ে ভাবতে হবে। ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের প্রসার ঘটে।
এ সময় শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত ‘ইউসুফ জুলেখা’ কাব্য সুলতান গিয়াস উদ্দিন আজম শাহ-এর রাজত্বকালে লিখিত হয়। কাব্যটি নবি ইউসুফের সংক্ষিপ্ত কাহিনি। গৌড় সুলতান ইউসুফ শাহের সভাকবি জৈনুদ্দিন ‘রসূল বিজয়’ কাব্য রচনা করেন। দৌলত উজির বাহরাম খাঁ রচিত লায়লী মজনু ফারসি কবি আবদুর রহমান জামির কাব্যের ভাবানুবাদ। মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতান এর কাব্য নবি বংশ, নসরুল্লাহ খাঁ রচিত পুঁথি কাব্য ‘জঙ্গনামা’ উল্লেখযোগ্য।
বিশ শতকের শুরুতে বাংলার মুসলিম কবি লেখকদের সাহিত্যচর্চা উল্লেখযোগ্য। গোলাম মোস্তফা রচিত বিশ্বনবি শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থগুলোর অন্যতম। সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মহাকবি কায়কোবাদ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, এস ওয়াজেদ আলী, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী উল্লেখযোগ্য।
ইসলামি কবিতা ও গান গজল রচনায় কাজী নজরুল ইসলামের অবদান চিরস্মরণীয়।
১৯ শতক পর্যন্ত তুর্কি সাহিত্য ফারসি ইসলামি ঐতিহ্যে পরিপুষ্টি লাভ করে। দেওয়ানি সাহিত্য ছিল উচ্চতর সাহিত্য। যা উসমানীয় দরবারের চারপাশে বিকাশ লাভ করে। এ শতকে তানযিমাত যুগের সঙ্গে তুর্কি সাহিত্যের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে। পশ্চিমা ফরাসি সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব শুরু হয়ে যায়। আরবি ফারসি উর্দু বিশ্বজনীন সমৃদ্ধ সাহিত্য হওয়া সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের কবি ও অপরাপর সাহিত্য শিল্পীরা এসব সাহিত্যের চর্চা ও অনুসরণে উদাসীন। অথচ সৈয়দ মুজতবা আলী তার বিখ্যাত উপন্যাস ‘শবনম’-এর মধ্যে দুর্লভ কিছু ফারসি প্রেমের বয়েত উল্লেখ করেছেন। যা পাঠককে বিস্মিত করে। যেমন :
কবি কিসাই ফুল সম্বন্ধে বলেন-
ওগো ফুলওয়ালী, কেন ফুল বেচো তুচ্ছ রূপার দরে?
প্রিয়তর তুমি কী কিনিবে, বলো, রূপো দিয়ে তার তরে?
কবি হাফিজের উদ্ধৃতি :
পরিপূর্ণতা পাবে তুমি কোথা ইরান দেশের ভূঁয়ে,
মেহদির পাতা কড়া লাল হয় ভারতের মাটি ছুঁয়ে।
ফারসি আরেকটি কবিতাংশ :
গোড়া আর শেষ এ সৃষ্টির জানা আছে, বলো, কার?
প্রাচীন এ পুঁথি গোড়া আর শেষে পাতা কটি ঝরা তার।
আমরা শুরু থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রধান ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ এবং আধুনিকতার সংক্ষিপ্ত ও প্রয়োজনীয় চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। ইতিহাস বলে, আরবি ফারসি উর্দু সাহিত্যের কদর পাশ্চাত্যে অনুভূত হলেও প্রাচ্যে তা কেন অবহেলিত? মধ্যপ্রাচ্যের সাহিত্য নিয়ে প্রযোজিত বহু চলচ্চিত্র বাংলাদেশে জনপ্রিয়।সেসব মূল্যবান সাহিত্য আদর্শ বাংলা ভাষী কবি লেখকদের চর্চার বাইরে কেন?
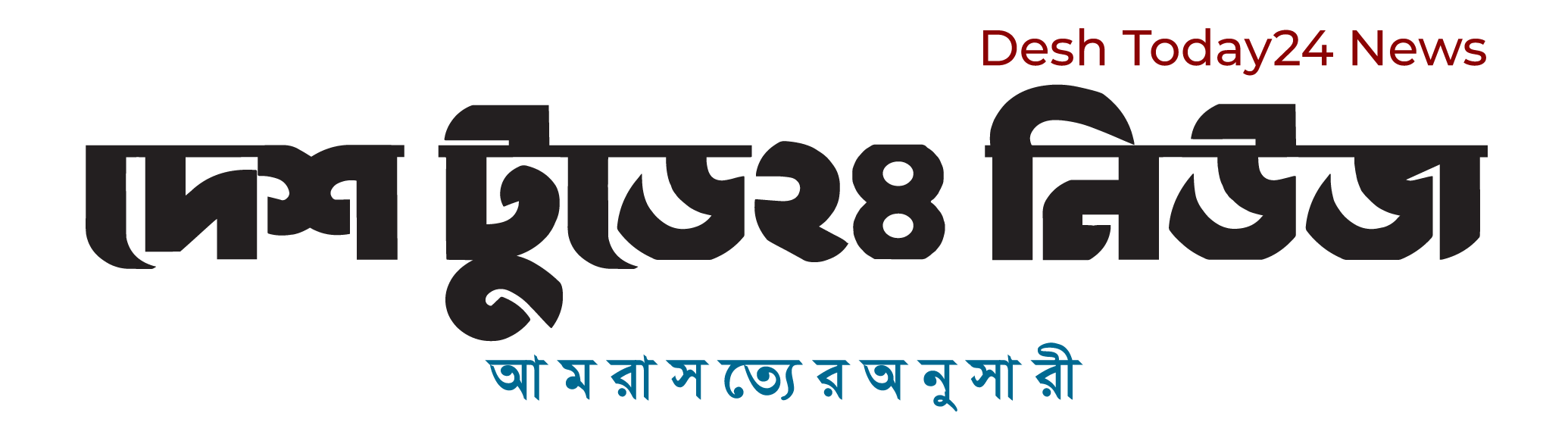
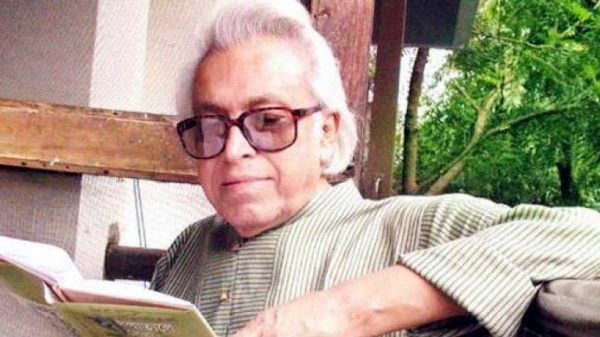















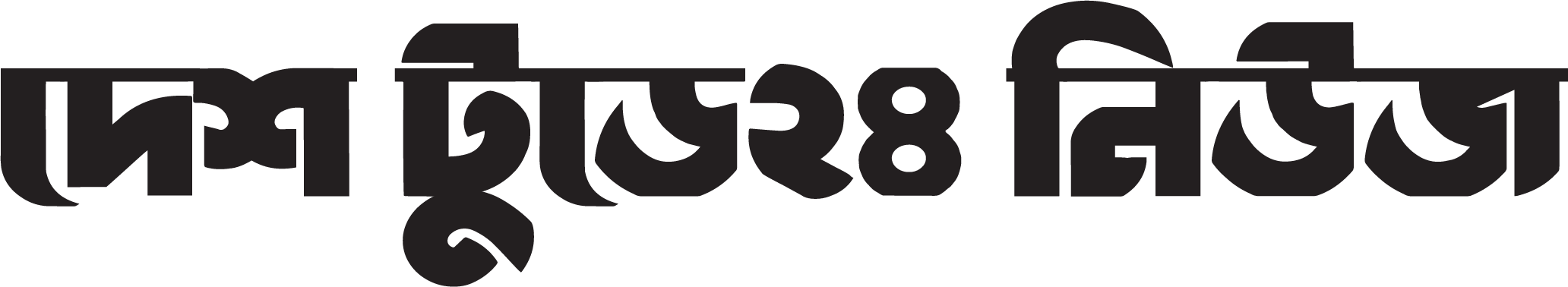
Leave a Reply